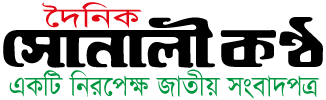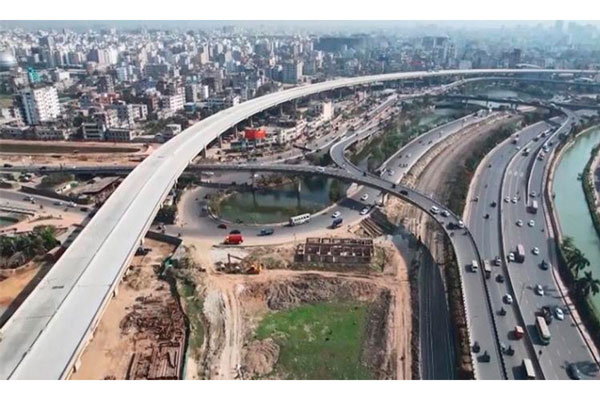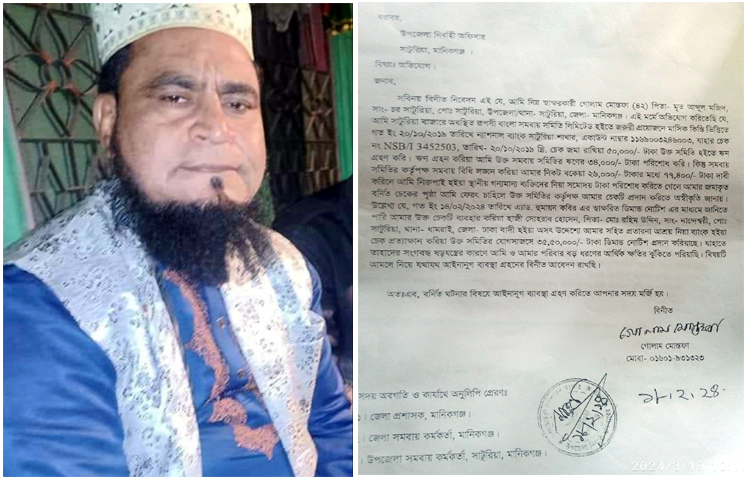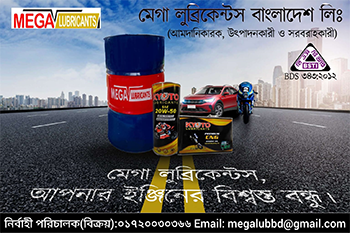- প্রকাশিত : ২০২৫-১০-১২
- ৩৯ বার পঠিত
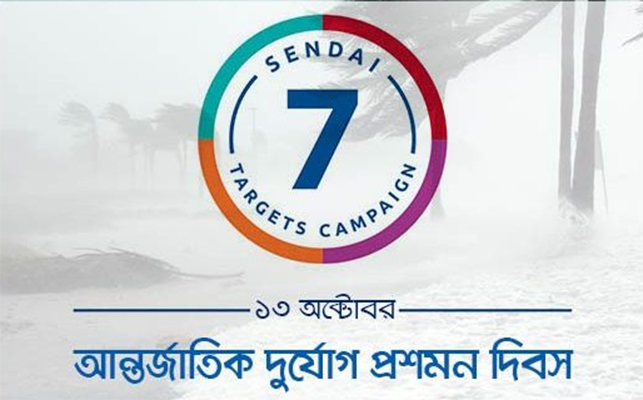
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
মানবসভ্যতার ইতিহাস প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে জীবন, খাদ্য, পানি, বাতাস, আলো ও সৌন্দর্য। কিন্তু এই প্রকৃতি মাঝে মাঝে রূপ নেয় ভয়াল রূপে—ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড, খরা কিংবা মহামারি—যা মানুষের জীবন, সম্পদ ও সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এসব দুর্যোগ পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব না হলেও, পরিকল্পিত প্রস্তুতি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সচেতনতা মানুষের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমাতে পারে। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় দুর্যোগ প্রশমন, অর্থাৎ দুর্যোগের ক্ষতি আগেভাগেই কমিয়ে আনা।এই বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে ঘোষণা করে যে, প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে পালিত হবে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। এর উদ্দেশ্য হলো—দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো, মানুষকে সচেতন করা এবং একটি স্থিতিশীল, নিরাপদ ও টেকসই সমাজ গড়ে তোলা।
> দিবসটির ইতিহাস
দুর্যোগ প্রশমনের ধারণা নতুন নয়। প্রাচীন যুগেও মানুষ বন্যা, ঝড় বা খরার আগে খাদ্য মজুত ও আশ্রয় তৈরির চেষ্টা করত। তবে এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এসেছে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ১৯৮০-এর দশকে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়ে যায়। বিশেষ করে—১৯৮৫ সালের মেক্সিকো সিটির ভূমিকম্প,১৯৮৮ সালের আর্মেনিয়ার ভয়াবহ ভূমিকম্প,এবং আফ্রিকার দীর্ঘস্থায়ী খরা—এই ঘটনাগুলো মানবসভ্যতাকে নড়িয়ে দেয়। জাতিসংঘ তখন সিদ্ধান্ত নেয়—বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ প্রশমনের প্রচেষ্টা জোরদার করা দরকার। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ১৩ অক্টোবর দিনটি হবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের আন্তর্জাতিক দিবস।
> দুর্যোগ প্রশমন মানে কী
‘প্রশমন’ মানে হলো ক্ষতি কমানো বা প্রভাব হ্রাস করা। অর্থাৎ, দুর্যোগ ঘটার আগে এমন প্রস্তুতি নেওয়া, যাতে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি যতটা সম্ভব কম হয়।চরম বন্যা, খরা, ঝড় ও তাপপ্রবাহের ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। পাশাপাশি এসব দুর্যোগে প্রতি বছর ৬৩ লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়।
দুর্যোগ প্রশমনের মূল ধাপগুলো হলো—
১. ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় শক্তিশালী ও টেকসই স্থাপনা নির্মাণ।
২. আগাম সতর্কতা ও উদ্ধার ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৩. জনগণকে প্রশিক্ষণ ও সচেতন করা।
৪. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
৫. ঝুঁকি-সহনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
অতএব, দুর্যোগ প্রশমন মানে শুধু ত্রাণ নয়; বরং দুর্যোগের আগে থেকেই বুদ্ধিদীপ্ত প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও দায়িত্বশীলতা।
> দিবসটির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য
এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে একটি সহনশীল ও টেকসই সমাজ গড়ে তোলা।দিবসটির লক্ষ্যসমূহ—
১. জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২. ঝুঁকি কমাতে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বাড়ানো।
৪. টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করা।
৫. মানবিক দায়বদ্ধতা ও পরিবেশ-সচেতনতা জোরদার করা।
দিবসটির বার্তা সহজ—দুর্যোগের পর নয়, আগে থেকেই প্রস্তুত হও।”
> বিশ্বে দুর্যোগের বাস্তবতা
জাতিসংঘের হিসাবে, প্রতিবছর গড়ে প্রায় চার শতাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। এসব ঘটনায় কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেকেই প্রাণ হারায় বা জীবিকা হারায়।
কিছু ভয়াবহ উদাহরণ—২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরের সুনামিতে প্রায় দুই লাখ ত্রিশ হাজার মানুষের মৃত্যু।২০১০ সালের হাইতি ভূমিকম্পে প্রায় দুই লাখ প্রাণহানি।২০২৩ সালে তুরস্ক ও মরক্কোর ভূমিকম্পে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি।এই উদাহরণগুলো দেখায়, আগাম সতর্কতা ও প্রস্তুতির ঘাটতি থাকলে দুর্যোগের ক্ষতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে।
> দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এখানে প্রায় প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, ভূমিধস, খরা ইত্যাদি ঘটে। তবুও বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ মোকাবিলায় সফলতার দৃষ্টান্ত।
সরকারি উদ্যোগসমূহ
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ – প্রতিরোধ ও প্রস্তুতির কাঠামো নির্ধারণ।
২. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০১৫ – টেকসই উন্নয়ন ও ঝুঁকি হ্রাসের সমন্বয়।
৩. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) – উপকূলে আগাম সতর্কতা ও উদ্ধার কার্যক্রম।
৪. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ – দ্রুত উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৫. কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা – জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততা।
৬. ১৪ হাজারেরও বেশি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ – উপকূলীয় মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
এসব পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় যেমন সিদর, আইলা বা মোখার সময় প্রাণহানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।
> শিক্ষা ও সচেতনতা
দুর্যোগ প্রশমনে শিক্ষা ও জনসচেতনতা অপরিহার্য। বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই শিক্ষার্থীদের শেখানো দরকার— * নিরাপদ আশ্রয় চিহ্নিত করা * প্রাথমিক চিকিৎসা শেখা * উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণের কৌশল জানা। * বাংলাদেশে এখন স্কুল নিরাপত্তা কর্মসূচি ও দুর্যোগ শিক্ষা ক্লাব চালু রয়েছে। এসব উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দুর্যোগের সময় সচেতন ও সাহসী করে তুলছে। * গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও স্থানীয় সংগঠনগুলোও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
> প্রযুক্তির ভূমিকা
* আজকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিনির্ভর।
* উপগ্রহ প্রযুক্তির মাধ্যমে আগাম সতর্কতা দেওয়া যায়। * ড্রোন ব্যবহার করে দুর্গম এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ করা সম্ভব। * মোবাইল বার্তার মাধ্যমে দ্রুত খবর পৌঁছে দেওয়া যায়। * মানচিত্রভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্ধারণ সহজ হয়েছে। * এসব প্রযুক্তির কারণে দুর্যোগ মোকাবিলা এখন অনেক বেশি দ্রুত, নির্ভুল ও কার্যকর।
> বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ
বিশ্বে দুর্যোগ প্রশমনের ক্ষেত্রে এখনো নানা প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে—
১. জলবায়ু পরিবর্তন ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি।
২. দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য।
৩. অপরিকল্পিত নগরায়ন ও জনসংখ্যার চাপ।
৪. অর্থনৈতিক ক্ষতি ও পুনর্গঠনের ব্যয়।
৫. রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব।
৬. তথ্য ও প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা।এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দরকার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা।
> আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নীতিমালা
২০১৫ সালে জাতিসংঘ গ্রহণ করে সেনদাই কাঠামো (২০১৫–২০৩০), যা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বৈশ্বিক রূপরেখা নির্ধারণ করেছে।
এর চারটি মূল লক্ষ্য হলো—
১. দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা।
২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো শক্তিশালী করা।
৩. দুর্যোগ প্রশমনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
৪. দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়া উন্নত করা।
এই নীতিমালা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, বিশেষত জলবায়ু ও নগর নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে।
> ভবিষ্যৎ করণীয়
দুর্যোগ প্রশমনকে সফল করতে হলে—
* স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। * পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। * শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্যোগ সচেতনতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। * নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা জোরদার করতে হবে।
* নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার ও গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। * আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তি বিনিময় বাড়াতে হবে।
* স্থানীয় সরকার পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
পরিশেষে বলতে চাই,প্রকৃতির রুদ্ররূপ ঠেকানো মানুষের সাধ্যের বাইরে, কিন্তু সচেতনতা, প্রস্তুতি ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা এর ক্ষতি অনেক কমাতে পারি।আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—দুর্যোগের ভয় নয়, প্রস্তুতিই আমাদের শক্তি।”
প্রকৃতির প্রতি অবহেলা, বনভূমি ধ্বংস ও নির্বিচারে পরিবেশ শোষণ একদিন মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে। তাই এখনই সময়—পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং প্রযুক্তিনির্ভর আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে একটি দুর্যোগ-সহনশীল, নিরাপদ ও টেকসই পৃথিবী।